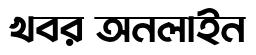পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়
হয়তো সারা জীবন তিনি মনে মনে একাকিনী একান্তেই গেয়ে গিয়েছেন, ‘আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় আমার মনে।/ সে আছে ব’লে/ আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,/ প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।’
১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ (১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট)। সতেরো বছরের মেয়েটির চোখে তখন শ্রাবণের ধারা। তার প্রাণের মানুষ, মনের দেবতার ফুলে ফুলে সাজানো দেহখানি নিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। কলেজ স্ট্রিটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে সে। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আর দেখা হল না। সে দিন তাঁর মহাপ্রস্থান ঘটেছিল জনসমুদ্রের কলকাতা শহরে। সারা বিশ্ব জুড়ে এক নিবিড় গভীর বেদনার সুর বেজেছিল সে দিন একটানা সবার মনে।
অবশ্য মেয়েটি ঠিক তার কুড়ি দিন পরে গিয়েছিল সেই দেবতার তীর্থস্থান শান্তিনিকেতনে। সে দিন সেখানকার গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সে দেখেছিল সেই নীরব হয়ে পড়ে থাকা পথখানি, যে পথ দিয়ে সেই মহামানব প্রতি দিন হেঁটেছেন। যেখানকার বাতাসে তাঁর সুর ভেসে বেড়ায় আজও। সেই পথের ধুলায় যেন সে দিনও সেই মেয়েটি শুনতে পেয়েছিল সেই সুর…‘আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন’ অথবা ‘এ পথে আমি যে গেছি বার বার, ভুলিনি তো একদিনও’।
যে মেয়েটির বাবা এক দিকে পুলিশ কোর্টের আইনজীবী, অন্য দিকে রবীন্দ্রস্নেহধন্য সাহিত্যিক। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তখন শ্যামবাজারের বাসিন্দা। দুই কন্যা, এক পুত্র এবং সন্তানসম্ভবা স্ত্রী সুবর্ণলতাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন ডেহরি-অন-সোন। ভ্রমণ শেষে ফিরছেন। ১৯২৪-এর ১৯ সেপ্টেম্বর। হঠাৎ স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, সঙ্গে ধুম জ্বর। একসময়ে ট্রেনেই মাতৃযন্ত্রণা উঠল। কিন্তু চলন্ত গাড়িতে চিকিৎসার কোনো উপায় নেই। অবশেষে সৌরীন্দ্রমোহনের বুদ্ধিমত্তায় এক অখ্যাত স্টেশনে ট্রেন থেমে গেল – গুঝান্ডি, শাল-পিয়ালের সবুজ মাখানো জায়গাটি। সেখানেই জন্ম নিল মায়ের কোল আলো করা মেয়ে, সুচিত্রা। বাবা আনন্দে আদর করে সদ্যোজাত সন্তানের ডাকনাম রাখলেন ‘গজু’, স্টেশনের নামের সঙ্গে মিলিয়ে।

উস্তাদ আমজাদ আলি খানের সঙ্গে।
বাবা আইনজীবী হলেও লক্ষ্মীর পেছনে ততটা ছোটেননি যতটা ছুটেছেন সরস্বতীর পেছনে। মাঝেমধ্যেই সংসারে টানাটানি পড়ত। এমনও দিন গিয়েছে যে, তেলের অভাবে শুধু মটরডালবাটা সেদ্ধ করে তা-ই দিয়েই ভাত খাওয়া হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে কোনো হাহুতাশ ছিল না পরিবারটির। বরং পরিবারে ছিল সাংস্কৃতিক বাতাবরণ। আর ছিল ছোট্টবেলা থেকে গজুর দামালপনা দুষ্টুমি। বিরাট বড়ো পরিবার। একান্নবর্তী সংসারে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার অভিজ্ঞতা শৈশব থেকেই সুচিত্রার মধ্যে গড়ে তুলেছিল সহিষ্ণু মানসিকতা। পড়েছেন বেথুন স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাশাপাশি ছিল বাড়িতে ছিল গান-নাচ-অভিনয়ের পরিমণ্ডল। বসত গানের মজলিশ। আসতেন বহু গুণীজন। যেমন আকাশবাণী খ্যাত পঙ্কজ কুমার মল্লিক, বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশির ভাদুড়ী, প্রমথেশ বড়ুয়া, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, মুজফ্ফর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, মধু বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এর ফলে ছোটোবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে ওঠেন সুচিত্রা। গান, নাচ ইত্যাদির প্রতি ছিল খুব আকর্ষণ। গানের গলাটিও খুব সুন্দর। পরিবারের সকলের ইচ্ছা, সুরসাধনার জন্য সুচিত্রা শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় থাকুক। কিন্তু না, তা হল না। সুচিত্রা শান্তিনিকেতনে গেলেন, কিন্তু গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের ২০ দিন পর, ১৯৪১ সালের ২৭ আগস্ট। জীবনের একটা আক্ষেপ রয়ে গেল সুচিত্রার।
তখন শান্তিনিকেতন যেন বিগ্রহহীন মন্দির। শান্তিনিকেতনের সব যেন হয়ে গিয়েছে শ্রীহীন। তবু সুচিত্রার মনের শান্তি – তিনি নেই বটে, কিন্তু তিনি তো এখানেই ছিলেন একদিন, এটাই বড়ো সত্যি আজ। পাঁচ বছর সুচিত্রা ছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর কথায়, “শান্তিনিকেতনে শৈলজাদার হাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃত পাঠ শুরু হল। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছি ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর কাছেও। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে যিনি সর্বার্থে আমার গুরু, তিনি হলেন শান্তিদেব ঘোষ। সঙ্গীতভবনের শিক্ষার্থী হিসাবে…শিখেছি খেয়াল-ঠুংরি, ধ্রুপদ-ধামার, টপ্পা, তবলা।” এসরাজ শিখেছিলেন অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। শান্তিনিকেতনে গান, নাচ শেখার পাশাপাশি বাটিকের কাজ, কাঁচা মাটির পট তৈরি করা, চামড়ার কাজ ইত্যাদি রপ্ত করে একদিন সুচিত্রা পুরোদস্তুর এক শিল্পী হয়ে উঠলেন।
শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের স্নেহচ্ছায়া, মোহর (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা (অরুন্ধতী দেবী), সেবা মাইতির মতো বন্ধুদের ভালোবাসায় থেকে রবীন্দ্রনাথের গানে, সাহিত্যে একেবারে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন সুচিত্রা। শান্তিনিকেতনেই থাকাকালীন ১৯৪৫ সালে এইচএমভি থেকে বেরোল সুচিত্রার প্রথম গানের রেকর্ড – এক পিঠে ‘হৃদয়ের এ কূল, ও কূল, দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনী’ আর অন্য পিঠে “মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যামসমান’।

আকাশবাণীতে সংগীত পরিবেশনরত।
সেই গান মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মানুষ মগ্ন সুচিত্রার গানে। সুচিত্রার কণ্ঠ যেন মহাকর্ষ। অনন্য অমোঘ এক আকর্ষণ সেই কণ্ঠে সংগীতের উপস্থাপনায়। বাঙালির কাছে সুচিত্রা মিত্রের সেই কণ্ঠের ঐশ্বর্য এক ইতিহাস, এক অননুকরণীয় অধরা মাধুরী। তাঁর গানের প্রক্ষেপণে যেমন পাওয়া যায় এই বাংলার শ্যামল কোমল স্নিগ্ধতার শীতলপাটি, তেমনি পাওয়া যায় প্রতিবাদের তেজোদৃপ্ত বহ্নিদীপ্ততা। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের গানের সাহিত্যমূল্য না বুঝলে কিছুই হবে না।… তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুভব করতে হবে, আত্মস্থ করতে হবে, তবেই সার্থকতা আসবে।”
রুদ্র আবেগের তীক্ষ্ণতায়, কোমল-বিনম্র আবেগের স্নিগ্ধতায়, সুচিত্রা মিত্রের স্বভাব-চরিত্রের স্বাভাবিকতায় ছিল এক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, তার ব্যথা-বেদনায় কখনও গোপনে চোখের জলও মুছেছেন, আবার মানুষের ওপরে নেমে আসা অন্যায়-অবিচারে তাঁর প্রতিবাদ ছিল প্রকাশ্যে বজ্রকঠিন গর্জিত উচ্চারণে। রবীন্দ্রনাথের মানবতার আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। রবীন্দ্রচিন্তা, রবীন্দ্র-আদর্শ, রবীন্দ্রদর্শন সম্পৃক্ত ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গে সদাসর্বদা।
ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্ফর আহমেদের আত্মজীবনীমুলক লেখা ‘আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’ থেকে জানা যায় যে কলকাতায় সে সময়ে পার্টির অফিস বলতে ট্রাম কোম্পানির যে ইউনিয়ন অফিস তা খুলতে মাঝেমধ্যেই বাবার হাত ধরে আসতেন বালিকা সুচিত্রা মিত্র। সেই ধারার ধারাবাহিকতায় বেথুন স্কুলের মেয়ে, স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়া, শান্তিনিকেতনের স্বনামধন্যা সুচিত্রা মিত্রকে এই কলকাতা এবং তার আশেপাশের মফঃস্বল দেখেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (আইপিটিএ) সদস্য হিসাবে কল-কারখানার গেট-মিটিংয়ে, পথে পথে, গানে গানে, স্লোগানে মানুষের মিছিলে পায়ে পা মেলাতে। সাথি হিসাবে পেয়েছেন কায়ফি আজমি (শাবানা আজমির বাবা), হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী, তৃপ্তি মিত্র,বলরাজ সাহনি, ভীষ্ম সাহনি, পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর, মৃণাল সেন, এ কে হাঙ্গল, দীনা পাঠক, করুণা সেন (পরে বন্দ্যোপাধ্যায়/ সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী সিনেমায় অপু-দুর্গার মা সর্বজয়ার ভুমিকায় অভিনয় করেন), ঋত্বিক ঘটক, মনীশ ঘটক, সৌমেন ঠাকুর, রবিশঙ্কর, সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবি দীনেশ দাস, মণিকুন্তলা সেন, জলি কাউল, পুরণচাঁদ যোশী (পিসি যোশী), বিপ্লবী কল্পনা দত্ত (পরে পিসি যোশীর স্ত্রী) প্রমুখকে।

মোহরের (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে।
বন্যা-মহামারী-দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মানুষ যখন কাঁদছে, তখন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের হাতে হাত মিলিয়ে সামর্থ্য উজাড় করে তাদের সেবায় কাজ করে গিয়েছেন এই সব দিকপাল শিল্পী। সুচিত্রা মিত্র সেই অসহায় মানুষগুলির একজন হয়ে গিয়েছিলেন সেই সময়ে। ময়দানের মঞ্চে দেবব্রত বিশ্বাস হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন আর দৃপ্তমন্দ্রিত সাবলীল কণ্ঠে তরুণী সুচিত্রা কখনও গাইছেন ‘নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়’ অথবা ‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো’ কিংবা ‘বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে’, কখনও বা গাইছেন ‘দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে’ অথবা ‘চলো চলো হে শান্তি সেনানী’ কিংবা ‘অনশন বন্দি ওঠোরে যত, জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত’ ইত্যাদি।
কলকাতার ডেকার্স লেনে সুচিত্রার গান শুনে বাগ্মী সাহিত্যিক ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “সে বেশ গলা ছেড়ে, পুরো দমে গান গায়। এর মধ্যে কোনও গোঁজামিল নেই। তার সাবলীলতা – সে একটা দেখার এবং শোনার জিনিস বটে।…সুচিত্রা নিখুঁত।”
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সংস্কৃতির যে মূল প্রেক্ষিত, তার সঙ্গে সুচিত্রা মিত্র অনায়াসে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন আপামর সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ এবং তার অধিকারের সংগ্রামকে। সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল সুর ও বাণীর ললিত সংগীতের সৌন্দর্যের রবি ঠাকুর আর তেজোদৃপ্ত রুদ্রদৃপ্ত গণসংগীতের প্রতিবাদের সুর।
রবীন্দ্রনাথের ‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি’-র মতোই সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে ইতিহাস হয়ে গিয়েছে সলিল চৌধুরীর লেখা ও সুরে রচিত একটি গান, যেখানে লেখা হয়েছে এই বাংলার কোনো এক ময়নাপাড়ার অভাবী কৃষ্ণকলি মেয়ের কথা, যার জীবন কেটে যায় দারিদ্র্যের ক্লান্তিতে পথ চলতে চলতে। সেই মেয়ে যখন কোনো অন্যায় অশোভন কিছুর সম্মুখীন হয়, তখন তার চোখে জ্বলে ওঠে ক্রোধের আগুন। সেই অভিব্যক্তির প্রকাশ নিয়ে তৈরি সলিলের এই গানেও সুচিত্রা মিত্রের উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে।
জীবনের নানা চড়াই-উতরাই, বিভিন্ন রকম টানাপোড়েনের জন্য হয়তো তিনি রাজনীতির পথে চলতে পারেননি। কিন্তু আজন্ম বাম-মনস্কতার সুচিত্রা মিত্রকে কোনো প্রলোভন বা কোনো রক্তচক্ষু বামপন্থী আদর্শ থেকে তিলমাত্র সরাতে পারেনি। অনেক রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিতা, কলকাতার শেরিফ, বাংলা ও বাঙালির মনে চিরভাস্বর হয়ে অধিষ্ঠিতা রবীন্দ্রসংগীতের সম্রাজ্ঞী এবং এ দেশের গণসংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ সুচিত্রা মিত্র ২০১১ সালের ৩ জানুয়ারি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তে হয়তো বলেছিলেন তাঁর জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের সেই শাশ্বত বাণী – ‘তবু মনে রেখো যদি দূরে চলে যাই’।
আজন্ম রবীন্দ্র-নিবেদিতা ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। কোনো নীচতা থেকে, কোনো ক্লীবতা থেকে যিনি ছিলেন শত সহস্র আলোকবর্ষ দূরে। যিনি ছিলেন তাঁর সারা জীবনের লালিত আদর্শের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় একাত্মতায় আবদ্ধ। তিনি জীবিত থাকলে আজকের এই উদ্ভ্রান্ত নষ্ট-ভ্রষ্ট সময়ে, উচ্ছিষ্টলোভী বুদ্ধিমানদের জটলাকে ঘৃণায় ধিক্কার জানাতে অগ্রণীর ভুমিকা নিতেন, এই আস্থা আমাদের বিশ্বাসকে জাগ্রত করে রাখে। আজকের এই দেশে, এই বাংলায় শঠতা, নীচতা, ধর্ম-জাতের বিদ্বেষে, হিংস্রতায়, এক চরম চৌর্যবৃত্তির লাগামছাড়া বেসাতির পরিমণ্ডলে তিনি মহানক্ষত্রের মতো বলে উঠবেন – সততার পথই হোক মহামন্ত্র। তাই ডাক দিয়ে যাই সকলকে, সৎ হও। আর ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে’। আর বলো, গীতবিতানই হল আমার একমাত্র গীতা, একমাত্র কোরান, একমাত্র বাইবেল, ত্রিপিটক। আমার কোনো ঠাকুর নেই, আমার ঠাকুর একজনই, তিনি ভারত-আত্মা, বিশ্ব-আত্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর কালজয়ী সৃষ্টি গীত ও নিবেদিত হয়েছে আজ থেকে ১৪০ বছরের বেশি আগে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণে।
জন্মভুমির, মাতৃভুমির এই নিকষ কালো অন্ধকার দিনে, এই উন্মত্ততায় বিভোর করা দুঃসময়ে, মানবাত্মার পূজারিনি সুচিত্রা মিত্রের জন্মশতবর্ষ-এর সন্ধিক্ষণে আমাদের সবার অন্তরে অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব শুভ মননে উচ্চারিত হোক রবীন্দ্রসংগীতে সমর্পিতা, আমাদের সকলের সম্মানিতা সমাদৃতা সেই সুচিত্রা মিত্রেরই নিবেদন – ‘অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো/ সেই তো তোমার আলো।/ সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো/ সেই তো তোমার ভালো।/…বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি/ সেই তো স্বর্গভূমি।/ সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি/ সেই তো আমার তুমি।’
আরও পড়ুন
মুক্তির মন্দির সোপানতলে: জুলিয়াস ফুচিক আজও যেন গেয়ে চলেছেন জাগরণের গান, বিপ্লবের গান